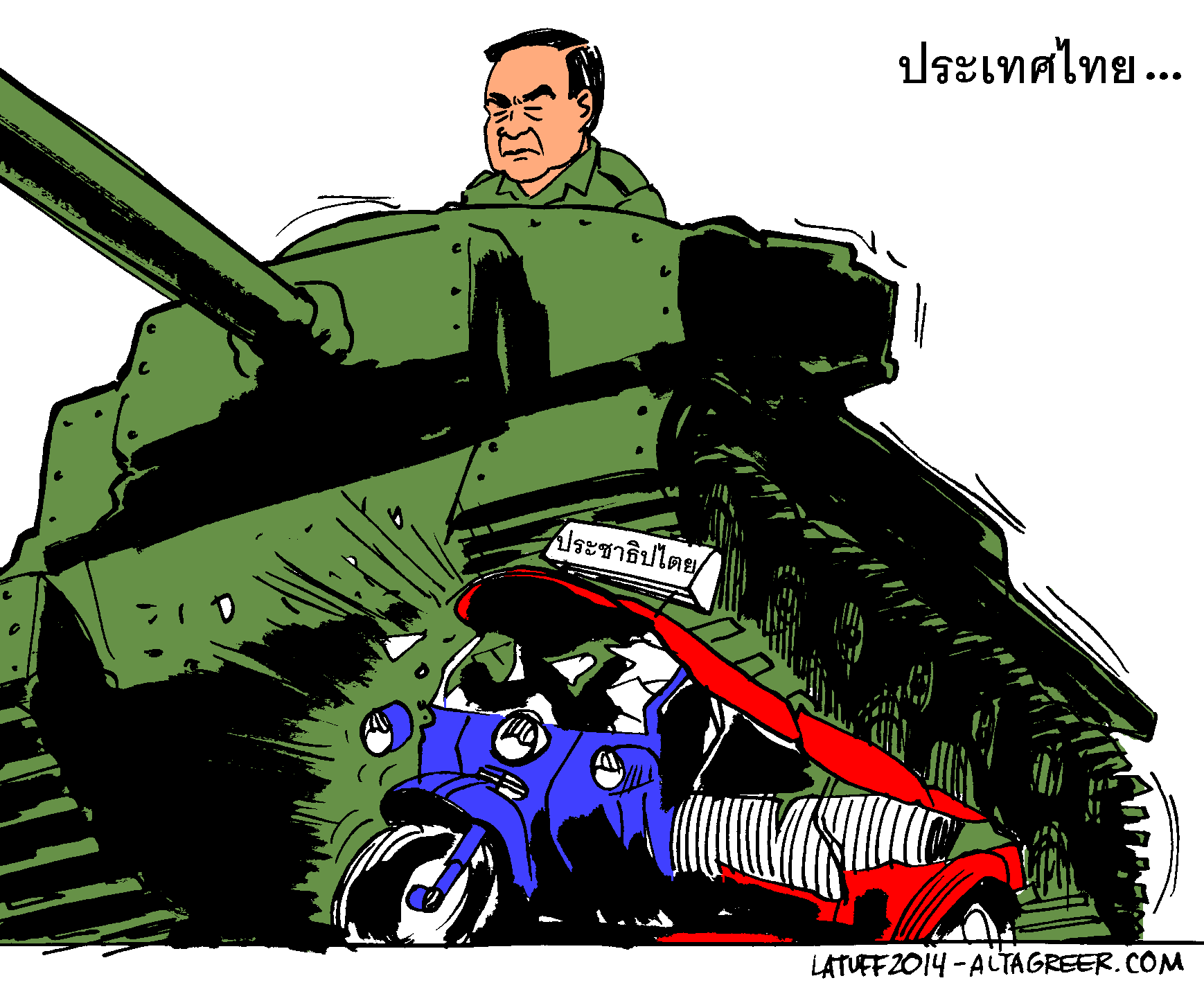শেষ
পর্যন্ত থাইল্যান্ডে সামরিক অভ্যুত্থানই হল। দেশটির চলমান সংকট কাটাতে
সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল প্রাইউথ সান-ওসার উদ্যোগে সরকারি ও বিরোধী দলের
মধ্যকার আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়, তখন সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। একই সঙ্গে
সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং সেনাপ্রধান নিজেকে অন্তর্বর্তীকালীন
প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন। গত ৬ মাস ধরে সেখানে সংকট চলে আসছে। এ সংকট আরও
গভীর হয় যখন ৭ মে দেশটির সাংবিধানিক আদালত প্রধানমন্ত্রী ইংলাক
সিনাওয়াত্রাকে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বরখাস্ত করে।মূলত সংকটের
শুরু ২০১৩ সালের অক্টোবরে, যখন ইংলাকের বড় ভাই ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী
থাকসিন সিনাওয়াত্রার দায়মুক্তির বিল সংসদে উপস্থাপন করা হয়। এ বিল নিয়ে
দেশে বড় বিতর্কের জন্ম হয়। নভেম্বরে সংসদের নিুকক্ষে দায়মুক্তি বিলটি পাস
হলেও উচ্চকক্ষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়। দায়মুক্তি বিলের প্রতিবাদে ব্যাংককে
লক্ষাধিক লোকের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে থাইল্যান্ডে দিনের পর দিন
বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। এমনকি বিক্ষোভকারীরা শহরের রাস্তাঘাট দখল করে
অবস্থান করে আসছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই
ফেব্র“য়ারিতে (২০১৪) প্রধানমন্ত্রী ইংলাক একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঘোষণা
দেন। কিন্তু তা বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এখানে বলা ভালো, ২
ফেব্র“য়ারি (২০১৩) থাইল্যান্ডে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ক্ষমতাসীন
পুয়ে থাই পার্টি বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় থেকে গিয়েছিল। প্রধান বিরোধী দল
ডেমোক্রেটিক পার্টি ওই নির্বাচন বয়কট করেছিল।যারা থাইল্যান্ডের
রাজনীতির কিছুটা খোঁজখবর রাখেন, তারা জানেন সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে
বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব বারবার সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। ইতিহাস বলে,
১৯৩২ সালে থাইল্যান্ডে প্রথম সেনা অভ্যুত্থান হয়েছিল। আর সর্বশেষ (১১তম)
সেনা অভ্যুত্থান হয় ২০০৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। তবে এই সেনা অভ্যুত্থান একটি
ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। সাবেক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার
সরকারের বিরুদ্ধে সেনাপ্রধান জেনারেল সোনধি বুজিয়ারাতসিনন ওই অভ্যুত্থানের
নেতৃত্ব দেন। অতীতে দেখা গেছে, সেনানায়করা রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে নিজেরা
ক্ষমতায় থাকার জন্য একটি দল গঠন করেন। কিন্তু সোনধি তা করেননি। তিনি একটি
নির্বাচনের আয়োজন করেন। কিন্তু নির্বাচন সেখানে কোনো রাজনৈতিক সমাধান বয়ে
আনতে পারেনি। ২০০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডে যে সাধারণ নির্বাচন
অনুষ্ঠিত হয় এবং যার তত্ত্বাবধান করেন জেনারেল সোনধি, তাতে বিজয়ী হয়ে
প্রধানমন্ত্রী হন সামাক সুন্দারাভেজ। কিন্তু তিনি বিরোধী দলের কাছে
গ্রহণযোগ্য হননি। তিনি পদত্যাগ করেন। তার পরিবর্তে পরে প্রধানমন্ত্রীর
দায়িত্ব নিয়েছিলেন সোমচাই ওয়াংসোয়াত। সুন্দরাভেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল
তিনি সিনাওয়াত্রার খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি দায়িত্ব নিলে প্রায় ৩ মাস ধরে
বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবন দখলসহ সরকার উৎখাতের আন্দোলন করে আসছিল। এর
নেতৃত্বে ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টি। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালয় পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী দেশে জরুরি অবস্থা জারি
করেও বিক্ষোভ দমন করতে পারেননি। ওই সময় সেনা অভ্যুত্থানের একটি সম্ভাবনার
জন্ম হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে সেনাপ্রধানের চাপে প্রধানমন্ত্রী
সোমচাই ওয়াংসোয়াত পদত্যাগ করেছিলেন এবং বিরোধী দলের নেতা অভিজিত ভেজাজিভার
নেতৃত্বে সেখানে একটি সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি
কখনও। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০০৬ সালের সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে
সিনাওয়াত্রার থাই রক থাই পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সিনাওয়াত্রার
সমর্থকরা পিপলস পাওয়ার পার্টি (পিপিপি) গঠন করে ২০০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বরের
সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল এবং বিজয়ী হয়েছিল। ওই নির্বাচনে ৪৮০টি আসনের
মাঝে পিপিপি ২৩২টি আসন পেয়েছিল। পিপিপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও
তারা একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিল। পিপিপি যেহেতু জনগণের ম্যান্ডেট
পেয়েছিল, সেহেতু তাদের টার্ম পূরণ করতে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি।
নির্বাচনের এক বছর পরই শুরু হয়েছিল সরকার উৎখাতের আন্দোলন। এখানে আরও একটি
বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন- সাংবিধানিক আদালত প্রধানমন্ত্রী সুন্দারাভেজকেও
অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। পরে ইংলাককেও অযোগ্য ঘোষণা করে এ আদালত।থাইল্যান্ডের
রাজনীতি এখন কার্যত দুভাগে ভাগ হয়ে আছে। একদিকে রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী
সিনাওয়াত্রার সমর্থকরা, যারা রেডশার্টধারী হিসেবে পরিচিত। থাকসিন
সিনাওয়াত্রার দল থাই রক থাই পার্টি নিষিদ্ধ হলে তার সমর্থকরা পিপলস পাওয়ার
পার্টির ব্যানারে আত্মপ্রকাশ করে। পরে তারা ইংলাক সিনাওয়াত্রার নেতৃত্বে
গঠন করে পুয়ে থাই পার্টি। এরা লালশার্ট পরিধান করে বিধায় তাদের আন্দোলনকে
রেডশার্ট আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে সিনাওয়াত্রাবিরোধীরা
ইয়েলো শার্টের ব্যানারে সংগঠিত, যে কারণে তারা ইয়েলো শার্ট আন্দোলনকারী
হিসেবে পরিচিত। এভাবেই থাইল্যান্ডের রাজনীতি লাল আর হলুদ শার্টের মাঝে ভাগ
হয়ে আছে। ইংলাক রেডশার্ট আন্দোলনকারীদের উসকে দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন। এটা
সত্য, জনগণের ভোটে তিনি বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ ছিল,
ভাইয়ের (থাকসিন সিনাওয়াত্রা) ছত্রছায়ায় তিনি ক্ষমতা পরিচালনা করে গেছেন।
থাকসিন সিনাওয়াত্রা থাইল্যান্ডের শীর্ষ ধনীদের একজন। তবে তার বিরুদ্ধে
দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। তার দেশে আসাও নিষিদ্ধ। ফলে ইংলাক যখন ভাইকে
দায়মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিল সংসদে আনেন, তখন তা বিতর্কের জন্ম
দেয়। এটা স্পষ্ট, অত্যন্ত ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী এ দায়মুক্তির বিরোধী। থাকসিন
সিনাওয়াত্রার সঙ্গেও সেনাবাহিনীর সম্পর্ক ভালো নয়।২০০৬ সালের সেনা
অভ্যুত্থানের পর একাধিকবার সেনা অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার জন্ম হলেও শেষ
পর্যন্ত তা হয়নি এবং সেনাবাহিনী ক্ষমতাও ধরে রাখেনি। সম্ভবত সেনা নেতৃত্ব
এটা বোঝেন যে, সেনা অভ্যুত্থান আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রচণ্ড
চাপের মুখে থেকেও সেনাবাহিনী ক্ষমতা ধরে রাখেনি। তারা সরকার পরিবর্তন
করিয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু ক্ষমতায় যায়নি। এখন ২০১৪ সালে এসে জেনারেল
প্রাইউথ সান-ওসার ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। কারণ থাইল্যান্ডে
সেনা অভ্যুত্থান এবং দীর্ঘদিন তাদের ক্ষমতায় থাকার ইতিহাস রয়েছে। বিংশ
শতাব্দীর পঞ্চাশ থেকে আশির দশকে পৃথিবীর অনেক দেশে (আফ্রিকা, লাতিন
আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য) সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সেনাশাসকরা
যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন (তুরস্কে মুস্তাফা কামাল, মিসরে নাসের,
আর্জেন্টিনায় পেরেন)। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে এ প্রবণতা কমতে থাকে এবং
আন্তর্জাতিক পরিসরে এর কোনো সমর্থনও নেই।থাইল্যান্ডে সেনাবাহিনী মূলত
একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছে। ব্যবসা, আমদানি-রফতানির সিংহভাগ
নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলরা (মিসরে এটা নিয়ন্ত্রণ করে
সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠানগতভাবে)। আর সম্ভবত সিনাওয়াত্রার সঙ্গে দ্বন্দ্বটা
তখন থেকেই শুরু। কারণ টেলিকমিউনিকেশন খাতসহ বেশ কিছু খাতের ব্যবসা
নিয়ন্ত্রণ করে সিনাওয়াত্রা পরিবার। ফলে সিনাওয়াত্রা ও তার বোন ইংলাক কখনোই
সেনাবাহিনীর কাছে গ্রহণযোগ্য হননি। এখানে সিনাওয়াত্রার একটা প্লাস পয়েন্ট
হচ্ছে, তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তার একটি সুদূরপ্রসারী
পরিকল্পনা ছিল। তিনি গ্রামের মানুষের কাছে জনপ্রিয়। তিনি সাধারণ মানুষের
উন্নয়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি
নিয়েছিলেন। ফলে তিনি নিষিদ্ধ হলেও তার সমর্থকদের (লালশার্ট আন্দোলন)
সাধারণ মানুষ বিপুল ভোটে বিজয়ী করেছিল। অন্যদিকে হলুদ শার্ট আন্দোলনকারীরা
যারা ডেমোক্রেটিক পার্টির ব্যানারে সংগঠিত এবং যাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর
সখ্য রয়েছে বলে ধরা হয়, তারা মূলত অভিজাততন্ত্র, ধনী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব
করে। ফলে স্পষ্টতই থাই রাজনীতি দুধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে।এটা বলতে
দ্বিধা নেই, সিনাওয়াত্রার আমলে থাইল্যান্ড যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, তা
থমকে গেছে। গত ৭-৮ বছরের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করা
যায়। এক. আইন অমান্য করার একটা প্রবণতা। যে সরকারই গঠিত হোক না কেন, তাকে
অস্বীকার করা যেন একটি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন হলেও
সরকার তার পাঁচ বছরের টার্ম পূরণ করতে পারছে না। দুই. বিক্ষোভকারীরা সরকারি
ভবন দখল করে, রাস্তায় দিনের পর দিন অবস্থান করে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার
যে বাজে প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, এটা থাই গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। তিন.
সেনাবাহিনীর প্রতিটি অ্যাকশন সিনাওয়াত্রা সমর্থকদের বিরুদ্ধে গেছে। এতে করে
একটা ধারণার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক- সেনাবাহিনী সিনাওয়াত্রাবিরোধীদের সমর্থন
করছে। চার. সেনাবাহিনী নিজেরা ক্ষমতা ধরে রাখতে চায় না। বিরোধীদের দমাতে
চায়। পাঁচ. সিনাওয়াত্রা সমর্থক ও বিরোধীদের মাঝে যদি কোনো সমঝোতা না হয়,
তাহলে রাজনৈতিক সংকট থেকে যাবেই। শুধু নির্বাচন দিয়ে এ সংকটের সমাধান করা
যাবে না। তাই জেনারেল প্রাইউথের দিকে দৃষ্টি থাকবে অনেকের- তিনি একটি দল
করবেন, নাকি নির্বাচন দিয়ে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ক্ষমতায নিয়ে
আসবেন?
থাইল্যান্ডের সামরিক অভ্যুত্থান যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে সমালোচিত হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি বলেছেন, এ অভ্যুত্থান গ্রহণযোগ্য নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নও এর সমালোচনা করেছে। থাইল্যান্ড আসিয়ানের সদস্য। আসিয়ান দেশগুলো থেকেও সমর্থন পাননি জেনারেল প্রাইউথ। উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এটা একটা বড় সমস্যা। খুব কম ক্ষেত্রেই এ দেশগুলো সত্যিকার গণতন্ত্র চর্চা করছে। কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের নামে একদলীয় তথা গোষ্ঠীতন্ত্র চালু হয়েছে। সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের যে স্পিরিট, তা বিকশিত হচ্ছে না। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশেও মোদির বিজয়ের মধ্য দিয়ে দেখা গেল কর্পোরেট হাউসগুলো, মিডিয়া ও অর্থ পরিবর্তনের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। মালয়েশিয়ার মতো দেশে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিংবা সিঙ্গাপুরের সংসদ পরিণত হয়েছে একদলীয় সংসদে, বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই। আর বাংলাদেশ কিংবা থাইল্যান্ডের মতো দেশে সরকার আর বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস আর আস্থার সম্পর্ক না থাকায় গণতন্ত্র এ দুটি দেশে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারছে না। বর্তমানে থাইল্যান্ডের গণতন্ত্র একটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যতদিন পর্যন্ত না জেনারেল প্রাইউথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করবেন, ততদিন থাইল্যান্ডে কোনো বিনিয়োগ হবে না। আমদানি-রফতানিতে ভাটা আসবে। আর আন্তর্জাতিক আসরে থাইল্যান্ডকে থাকতে হবে কড়া চাপের মুখে। থাইল্যান্ডে গণতন্ত্রের বিকাশ যতটুকু না রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভর করে, ততটুকু সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে না। সেনাবাহিনী নির্বাচন দেবে। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি বিজয়ী হয়ও (?), তারপরও সমস্যা থেকে যাবে। কেননা লালশার্ট আন্দোলনকারীদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আপাতদৃষ্টিতে তৃতীয় কোনো শক্তিকেও দেখা যাচ্ছে না রাজনীতির ময়দানে। জেনারেল প্রাইউথ কোনো তৃতীয় শক্তিকে সমর্থন দিয়ে তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন, তেমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ফলে থাইল্যান্ডের গণতন্ত্র নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন থেকে গেল। সামরিক বাহিনী ইংলাক সিনাওয়াত্রা কিংবা বিরোধী দলের নেতা সুথেপ থাউগসুবানকে গ্রেফতার করলেও থাইল্যান্ডের পরিস্থিতি শান্ত হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। Daily Jugantor ০১ জুন, ২০১৪
থাইল্যান্ডের সামরিক অভ্যুত্থান যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে সমালোচিত হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি বলেছেন, এ অভ্যুত্থান গ্রহণযোগ্য নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নও এর সমালোচনা করেছে। থাইল্যান্ড আসিয়ানের সদস্য। আসিয়ান দেশগুলো থেকেও সমর্থন পাননি জেনারেল প্রাইউথ। উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এটা একটা বড় সমস্যা। খুব কম ক্ষেত্রেই এ দেশগুলো সত্যিকার গণতন্ত্র চর্চা করছে। কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের নামে একদলীয় তথা গোষ্ঠীতন্ত্র চালু হয়েছে। সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের যে স্পিরিট, তা বিকশিত হচ্ছে না। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশেও মোদির বিজয়ের মধ্য দিয়ে দেখা গেল কর্পোরেট হাউসগুলো, মিডিয়া ও অর্থ পরিবর্তনের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। মালয়েশিয়ার মতো দেশে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিংবা সিঙ্গাপুরের সংসদ পরিণত হয়েছে একদলীয় সংসদে, বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্ব সেখানে নেই। আর বাংলাদেশ কিংবা থাইল্যান্ডের মতো দেশে সরকার আর বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস আর আস্থার সম্পর্ক না থাকায় গণতন্ত্র এ দুটি দেশে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারছে না। বর্তমানে থাইল্যান্ডের গণতন্ত্র একটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যতদিন পর্যন্ত না জেনারেল প্রাইউথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করবেন, ততদিন থাইল্যান্ডে কোনো বিনিয়োগ হবে না। আমদানি-রফতানিতে ভাটা আসবে। আর আন্তর্জাতিক আসরে থাইল্যান্ডকে থাকতে হবে কড়া চাপের মুখে। থাইল্যান্ডে গণতন্ত্রের বিকাশ যতটুকু না রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভর করে, ততটুকু সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে না। সেনাবাহিনী নির্বাচন দেবে। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি বিজয়ী হয়ও (?), তারপরও সমস্যা থেকে যাবে। কেননা লালশার্ট আন্দোলনকারীদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আপাতদৃষ্টিতে তৃতীয় কোনো শক্তিকেও দেখা যাচ্ছে না রাজনীতির ময়দানে। জেনারেল প্রাইউথ কোনো তৃতীয় শক্তিকে সমর্থন দিয়ে তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন, তেমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ফলে থাইল্যান্ডের গণতন্ত্র নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন থেকে গেল। সামরিক বাহিনী ইংলাক সিনাওয়াত্রা কিংবা বিরোধী দলের নেতা সুথেপ থাউগসুবানকে গ্রেফতার করলেও থাইল্যান্ডের পরিস্থিতি শান্ত হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। Daily Jugantor ০১ জুন, ২০১৪