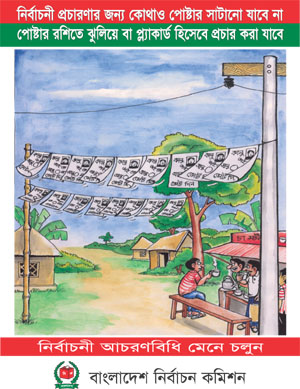
বাংলাদেশের দ্বাদশ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কেএম
নুরুল হুদা। তিনি দায়িত্ব নেবেন আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি। তার সঙ্গে আরও ৪ জন
কমিশনারও ওই দিন শপথ নেবেন। নয়া সিইসি এমন এক সময় দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন,
যখন বাংলাদেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমান
সরকারের মেয়াদ শেষ হবে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে। এর ৯০ দিনের আগেই এই
নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। আর নতুন নির্বাচন কমিশনের ওপরই দায়িত্বটি
বর্তাবে ওই নির্বাচন আয়োজন ও সম্পন্ন করার। পাঁচ বছরের জন্য নয়া সিইসি
দায়িত্ব পেয়েছেন। নয়া সিইসির জন্য দায়িত্বটি যে সহজ, তা বলা যাবে না।
বিএনপি বড় রাজনৈতিক দল। ইতিমধ্যেই বিএনপি যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা
সিইসিকে নিঃসন্দেহে অসন্তুষ্ট করে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিএনপি এই
কমিশনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি। বরং কিছুটা ‘রিজার্ভেশন’ রেখেই
বিএনপির নেতারা তাদের ‘অবর্জাভেশন’ রাখছেন। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও
বিএনপির অবর্জাভেশন দেখে তাই সঙ্গত কারণেই কতগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
যায়। প্রথমত, আমলাতন্ত্রনির্ভর যে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা আমাদের দেশে
জন্ম হয়েছে, তা থেকে আমরা এবারও বের হয়ে আসতে পারলাম না। ক্ষমতাসীন দলের
আমলাপ্রীতি আরও বেড়েছে। পাঁচজনের কমিশনে একজন সামরিক আমলাসহ ৪ জনই আমলা।
যাদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সার্চ কমিটি গঠন করে নির্বাচন
কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হলেও সিইসি নির্বাচন নিয়ে একটা ‘প্রশ্ন’ থেকে
গেলই। একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, এবার এমন একজন সিইসি হিসেবে
নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন, যিনি থাকবেন ‘সব বিতর্কের’ ঊর্ধ্বে। কিন্তু তেমনটি হল
না। কেএম নূরুল হুদা কমিশন রকিব কমিশনের মতোই শেষদিন পর্যন্ত সমালোচিত হতে
পারেন। তৃতীয়ত, সিইসি কেএম নূরুল হুদা বিতর্কিত ‘জনতার মঞ্চ’-এর সঙ্গে
সম্পৃক্ত বা সমর্থন করেছিলেন কিনা, এটা আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যদিও তিনি
বলেছেন, তিনি ওই সময় কুমিল্লার ডিসি ছিলেন এবং ‘জনতার মঞ্চ’ হয়েছিল
ঢাকাতে। তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তার কথাকে আমাদের ‘সত্য’ বলে ধরে
নিতে হবে। কিন্তু দুটি সংবাদ এখন সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে আছে, এর মাঝে
একটি আবার ছবি। উক্ত ছবিতে পটুয়াখালীতে স্থানীয় পর্যায়ের আওয়ামী লীগের
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাকে দেখা যাচ্ছে- ছবির ক্যাপশনের ভাষ্য এমনই। তার ভাই
আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা এমনটাই বলা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা স্বয়ং
সিইসি দিতে পারেন। কিন্তু তিনি দেননি। দ্বিতীয়টি একটি খবর- কুমিল্লায় ওই
সময় যে ‘জনতার মঞ্চ’ গঠিত হয়েছিল এবং ডিসি অফিস থেকে খালেদা জিয়ার (তখন
তিনি প্রধানমন্ত্রী) ছবি নামিয়ে নেয়া সম্পর্কিত। তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা
হয়েছে ভোরের কাগজ ৩০ মার্চ ১৯৯৬-এর সংখ্যাটি। বিএনপির রিসার্চ টিম (যদি আদৌ
থাকে) ওই সংখ্যার কাটিং এখন উপস্থাপন করতে পারে। চতুর্থত, সিইসি পদটি মূলত
সচিব পদমর্যাদার। তিনি যুগ্ম-সচিব হিসেবে বাধ্যতামূলক অবসরে (২০০১)
গিয়েছিলেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে ভূতাপেক্ষভাবে দুটো প্রমোশন
দেয়- একসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব। অর্থাৎ সচিব হিসেবে তিনি কখনও কাজ
করেননি। হাইকোর্ট, না প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তিনি চাকরি ফেরত
পেয়েছিলেন- এটা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি
সংবাদে বলা হয়েছে, তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দেয়া হাতেম আলী খানের
মামলার সূত্র ধরেই চাকরি ফেরত পেয়েছিলেন। পঞ্চমত, সার্চ কমিটির নামের
তালিকায় (সিইসির জন্য) তার নাম ছিল এবং আওয়ামী লীগের দেয়া তালিকায় তার নাম
ছিল না- দুটোই সত্য। কিন্তু ১৪ দলের শরিক দল তরীকত ফেডারেশন ও গণতন্ত্রী
পার্টির দেয়া তালিকায় তার নাম থাকায় তার নিয়োগ একটি ‘প্রশ্নের’ মাঝে ফেলে
দিয়েছে। সিইসি নিয়োগে ‘পরিকল্পিত না কাকতালীয়’ যে অভিযোগটি উঠেছে, তা আমরা
অস্বীকার করি কীভাবে? এমনকি কমিশনার হিসেবে কবিতা খানমের ব্যাপারেও একই
অভিযোগ উঠেছে। দেশে প্রচুর জেলা ও দায়রা জজ আছেন, যারা অবসরে গেছেন। তার
মাঝে এই একটি নাম ‘কমন’ পড়ল কীভাবে? ষষ্ঠ, সিইসি নিয়োগে বিএনপি সতর্ক
প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। আমার কাছে এর অর্থ পরিষ্কার। বিএনপি এই কমিশনকে
প্রত্যাখ্যান করবে না। বরং এই কমিশনের আন্ডারে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও
বিএনপি অংশ নেবে। কেননা নিবন্ধন হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে বিএনপি। পরপর দুটো
জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করলে বিএনপির নিবন্ধন বাতিল হতে পারে। সেজন্য
২০১৯ সালে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হতে
যাচ্ছে, তাতে অংশ নেয়া ছাড়া দলটির আর কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে বিএনপি
যা করবে, তা হচ্ছে বিএনপি চেষ্টা করবে বর্তমান সিইসির আওয়ামী লীগদলীয়
সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরে জনমত গড়ে তুলতে। সেই সঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তুতিও
গ্রহণ করবে দলটি। সপ্তমত, বিএনপি চেষ্টা করবে একটি ‘নির্বাচনকালীন
সরকার’-এর ধারণা নিয়ে জনমত সংগঠিত করতে। বিএনপির রিসার্চ টিম এটা নিয়ে কাজ
করতে পারে এবং এ বছরের কোনো এক সময় ‘নির্বাচনকালীন সরকার’-এর একটি রূপরেখা
উপস্থাপন করতে পারে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না বিএনপি দশম জাতীয় সংসদে না
থাকায় তার অবস্থান এখন বড় দুর্বল। সংবিধানে একটি নির্বাচনকালীন সরকারের
রূপরেখা দেয়া আছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রেখেই এই নির্বাচন
অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এখন বিএনপিকে এটা মেনে নিয়েই নির্বাচনে যেতে হবে। দশম
জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপি বয়কট করেছিল এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনের ডাক
দিয়েছিল। কিন্তু তা দলটিকে বড় বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সেই ‘সংকট’ থেকে
বিএনপি এখনও পুরোপুরিভাবে বের হয়ে আসতে পেরেছে- এটা মনে হয় না।
৯ ফেব্রুয়ারি যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন একটি
গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি বলেছেন, নির্বাচনকালীন সরকারের একটি রূপরেখা
রাষ্ট্রপতির কাছে দেয়া হয়েছে। তবে সেই রূপরেখাতে কী আছে, তা তিনি নিশ্চিত
করেননি। একটি কথা অবিশ্যি তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকবে,
তারা নীতিগতভাবে তখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। বড় কোনো প্রকল্প হাতে নেবে
না। অতীতে একটি নির্বাচনকালীন সরকার আমরা দেখেছি। ওই সরকারের পরিধি ছোট ছিল
এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব ছিল। কিন্তু বিএনপির
কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ধারণা করছি দিন যত যাবে, ততই আওয়ামী লীগের এই
‘পরিকল্পনা’ ব্যাপকভাবে আলোচিত হবে। এ ক্ষেত্রে বিএনপি চাচ্ছে
নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে সরকারের সঙ্গে একটি সংলাপ। এই সংলাপ
আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
রাষ্ট্রপতি বেশ ক’টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন গঠনের
যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে সেই
প্রক্রিয়া শেষ হল। কিন্তু এতে সব ‘প্রশ্নের’ জবাব আমরা পেয়ে গেছি, তা বলা
যাবে না। সংলাপে দাবি উঠেছিল নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য সংবিধানে যে আইনের
কথা বলা আছে (১১৮-১), সেই আইনটি দ্রুত তৈরি করার। সময়ের স্বল্পতার কারণে
এবার আইনটি করা গেল না বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ধারণা
করছি আইনটি হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় আইনটি যেন ‘বিতর্কিত’
না হয়ে যায়। কোনো বিশেষ দল, বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় আইনটি যেন তৈরি
না হয়, সে দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। আইনটি প্রণয়নে সব ‘স্টেকহোল্ডারদের’
অংশগ্রহণ, সুশীল সমাজের ভূমিকা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন। সরকারের সঙ্গে
রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় একজন নারী কমিশনারের অন্তর্ভুক্তির দাবি উঠেছিল।
সার্চ কমিটির সুপারিশেও দু’জন নারীর নাম ছিল। রাষ্ট্রপতি এদের একজনকে
নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু একজন অবসরপ্রাপ্ত দায়রা জজ নির্বাচন ব্যবস্থা,
রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কি কোনো ধারণা রাখেন? ফৌজদারি বিধি সম্পর্কে
তিনি জ্ঞাত। বিচার-আচার নিয়ে কাজ করে ৫৯ বছর বয়সে অবসরে গেছেন। এখন তিনি
নির্বাচন ব্যবস্থা তথা ‘সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচনী ব্যবস্থা’ নিশ্চিত
করতে কী অবদান রাখতে পারবেন, সে প্রশ্ন থাকলোই। শুধু নারী কমিশনারের কথা
কেন বলি? একজন সাবেক অতিরিক্ত সচিব, যিনি একজন কবিও বটে, মধ্যসত্তরে তার
বয়স। মানসিক ও শারীরিকভাবে তিনি কতটুকু ‘চাপ’ সইতে পারবেন, সেটাও একটা বড়
প্রশ্ন। আসলে যারা নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করেছেন, যাদের এ ব্যাপারে
যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে, তাদের নির্বাচন কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হলে নিশ্চয়ই
ভালো হোত। এমনকি একজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিকেও চেয়েছিলেন সার্চ কমিটির
অন্যতম সদস্য সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে তা গুরুত্ব
পায়নি। বলা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টা সিরিয়াসলি নেননি। কেননা নয়া
নির্বাচন কমিশন গঠনে তার ভূমিকা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সিইসিসহ ৪ জন
কমিশনারের নাম তিনি ‘ক্লিয়ার’ করেছিলেন। আর তার সবুজ সংকেত পাওয়ায় তাদের
নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে। সংবিধানের ৪৮(৩) ধারা মতে, রাষ্ট্রপতি দুটো কাজ বাদে
(প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ) বাকি সব কাজে প্রধানমন্ত্রীর
পরামর্শ নিতে বাধ্য। এখন সার্চ কমিটি ১০ জনের নামের তালিকা দিয়েছিল এবং
সেখান থেকে যে ৫ জনের তালিকা (সিইসিসহ) চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানে
প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছিল এবং তার সম্মতি নিয়েই এদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
এদের কোনো একজনের ক্ষেত্রে যদি প্রধানমন্ত্রীর ‘আপত্তি’ থাকত, তিনি নিয়োগ
পেতেন না।
সিইসি ইতিমধ্যে ‘কথা’ বলতে শুরু করেছেন। মিডিয়া তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে,
এটা স্বাভাবিক। তিনি ভালো করতেন, যদি তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেয়ার পর
কথা বলতেন। আর একটা কথা- মিডিয়াতে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল। এভাবে
প্রতিদিন মিডিয়ার সম্মুখে বক্তব্য রাখা ঠিক নয়। সাংবিধানিক পদে যারা থাকেন
তারা এভাবে মিডিয়ায় আসেন না। মিডিয়া আগ্রহী হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু
বারবার মিডিয়াতে আসা ঠিক নয়। নির্বাচন কমিশনের যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে
তা বলবে নির্বাচন কমিশনের সচিব, মুখপাত্র হিসেবে। নয়া ইসির দায়িত্ব এখন
অনেক বেশি। তাদের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ভোটাররা নির্বাচন
ব্যবস্থার উপর যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, তা তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।
নির্বাচনী ব্যবস্থায় ‘ফেনী মডেল’ নির্বাচনী সংস্কৃতির জন্য একটি ‘কালো
অধ্যায়’। এই ‘ফেনী মডেল’ আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতিকে ‘খাদের কিনারে’ নিয়ে
গেছে, অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ‘ফিসক্যাল ক্লিফ’ (Fiscal
Cliff) পরিস্থিতির মতো (ডিসেম্বর ৩১, ২০১২)। সমঝোতা না হলে গভীর খাদে পরে
যাওয়ার মতো পরিস্থিতি! আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা অনেকটা সেই পর্যায়ে চলে
গেছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন প্রার্থীর বিজয়ী হওয়া, ৫২ ভাগ
জনগোষ্ঠীর ভোট দিতে না পারা সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী) কিংবা
বিরোধী প্রার্থীদের ভোট কেন্দ্র্রে উপস্থিত হতে না দেয়া (ফেনী মডেল)
ইত্যাদি আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতির একটি ‘কালো দিক’। নয়া কমিশন নিশ্চয়ই এই
বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা রাখে। তাই তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক
বেশি। ‘সব দলের অংশগ্রহণে’ একটি নির্বাচনী সংস্কৃতি ফিরে আসুক এ দেশে। যারা
নির্বাচন ব্যবস্থাকে ভণ্ডুল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে
হবে। সংবিধানের ১১৮(৪) ধারা মতে, নির্বাচন কমিশন তাদের কর্মকাণ্ডে যে
‘স্বাধীন’, তা তাদের প্রমাণ করতে হবে। ১২১ ধারা মতে, প্রতি এলাকার জন্য
একটি মাত্র ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। সিইসি ও কমিশনাররা স্বচ্ছতার
স্বার্থে তাদের ‘আয়কর রিটার্ন’ প্রকাশ করতে পারেন। তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ
হচ্ছে সব দলের আস্থা অর্জন। দায়িত্ব নেয়ার পর তারা দলগুলোর সঙ্গে ‘সংলাপ’ও
করতে পারেন।
Daily Jugantor
13.02.2017
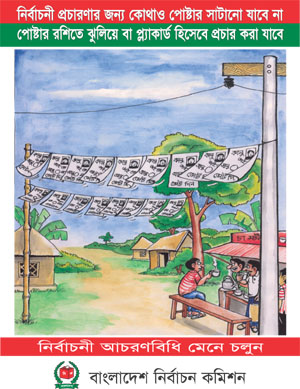






0 comments:
Post a Comment