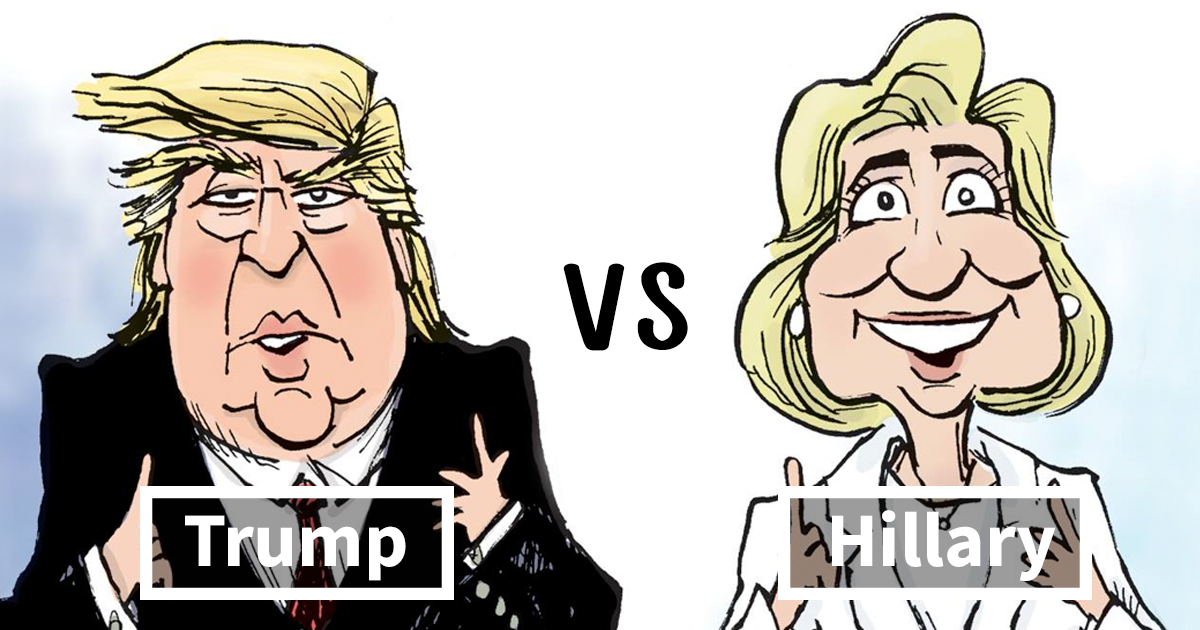কিউবার বিপ্লব, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এককভাবে ‘সংগ্রাম’ করার নাম ফিদেল কাস্ত্রো। আমাদের মতো তরুণ প্রজন্ম সত্তর-পরবর্তী সময়ে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, আমাদের কাছে ‘আদর্শ’ ছিল দুজন চে গুয়েভারা ও ফিদেল কাস্ত্রো। দুজন বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। বিপ্লবের পর কিউবার মন্ত্রীও হয়েছিলেন চে। কিন্তু ক্ষমতা ধরে রাখেননি। বিপ্লব সম্পন্ন করতে ছুটে গিয়েছিলেন বলিভিয়ায়। সেখানে চে-কে বলিভিয়ার সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে। একজন ডাক্তার, লেখক এবং সর্বোপরি একজন বিপ্লবী চে কিউবা ছেড়ে যাওয়ার আগে কাস্ত্রোকে উদ্দেশ করে একটি আবেগময় চিঠি লিখেছিলেন। ভাষাটা ছিল এরকমÑ ‘বিপ্লব আমাকে ডাকছে। আমার অনেক কাজ বাকি। স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে যাচ্ছি। জানি রাষ্ট্র এদের দেখভাল করবে!’ অনেকটা এরকমই ছিল ভাষা। একজন বিপ্লবী কতটুকু ‘ডেডিকেটেড’ হলে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন না। চে করেছিলেন। তাই চে আজও আদর্শ। চে’র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ফিদেল। ফিদেল কিউবায় ‘সমাজতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার জন্য থেকে গিয়েছিলেন। সেই ফিদেল, জলপাই রঙের আউটফিট, মাথায় জলপাই রঙের টুপি, কোমরে মোটা বেল্টÑ একজন বিপ্লবীর ছবি মানেই যেন ফিদেল কাস্ত্রো। সেই ফিদেলকে দেখার শখ ছিল আমার। সুযোগ এসেছিল ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসেছিল নিউইয়র্কে। আমি তখন নিউইয়র্কে। বিশেষ ‘পাস’ সংগ্রহ করে দর্শক সারিতে বসে ফিদেল কাস্ত্রোকে সেদিন দেখেছিলাম। কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম আমি। সেদিন ফিদেল জলপাই রঙের আউটফিট নিয়ে জাতিসংঘে আসেননি। এসেছিলেন স্যুটেড-বুটেড হয়ে। তবে আমার ভালো লেগেছিল একটি সংবাদেÑ কাস্ত্রো কোনো পাঁচ তারকা হোটেলে রাত্রি যাপন করেননি। তিনি রাতে ছিলেন কিউবার রাষ্ট্রদূতের বাসায়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের সরকারপ্রধানরা থেকেছিলেন পাঁচ তারকা হোটেলে! কাস্ত্রোও থাকতে পারতেন। থাকেননি।
কিউবার বিপ্লবের অনেকগুলো দিক আছে। প্রথমত, তৎকালীন বাতিস্তা সরকারের দুর্নীতি, অযোগ্যতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা ও স্বৈরাচারী মনোভাব, গুম-হত্যার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভটি বিপ্লবীরা ব্যবহার করেছে এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা কিউবার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবীরা কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না প্রথমদিকে। ঞযব সড়াবসবহঃ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে তারা সংগঠিত হয়েছিলেন। পরে পর্যায়ক্রমে ১৯৬৫ সালে তারা কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হন। তৃতীয়ত, বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে কাস্ত্রো যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন (এপ্রিল ১৯৫৯)। উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রে তার সমর্থনে জনমত সংগ্রহ করা। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের স্পষ্ট করে বলেছিলেন, তিরিন কমিউনিস্ট নন। ফলে কিউবার বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করা। মূলত ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি কিউবায় বাতিস্তা সরকারের পতনের কিছুদিন আগে ১৯৫৩ সালে এই বিপ্লবের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবে এটা সত্য কাস্ত্রো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করতে চাননি। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি এই সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। কিউবার বিপ্লবের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, জেনারেল বাতিস্তার শাসনামলের শেষের দিকে বাতিস্তার শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে একজন আইনজীবী হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রো আদালতে একটি আর্জি পেশ করেছিলেন। কিন্তু তার সেই আর্জি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এর পরই তিনি সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা থেকে বাতিস্তাকে উৎখাতের উদ্যোগ নেন। প্রথমদিকে ১২০০ যুবককে নিয়ে তিনি একটি ব্রিগেড গঠন করেছিলেন। এই ব্রিগেড সদস্যদের নিয়ে ১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই সান্টিয়াগো শহরের মনসাদা ব্যারাক ও বেয়ামো সেনাক্যাম্প আক্রমণ করেন। এতে তিনি ব্যর্থ হন। গ্রেপ্তার হন। তার ১৫ বছরের জেল হয়। আবার ১৯৫৫ সালে তিনি মুক্তিও পান। এর পর তিনি বিপ্লবকে সংগঠিত করতে চলে যান মেস্কিকোয়। এর পর শুরু হয় চূড়ান্ত বিপ্লবের প্রক্রিয়া। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে গ্রানমা জাহাজে করে ৮০ বিপ্লবীকে নিয়ে তিনি ফিরে আসেন কিউবায়। ‘সিয়েরা মায়েস্ত্রা’ পাহাড়ে আশ্রয় নেন বিপ্লবীদের নিয়ে। সেখান থেকেই বিপ্লব পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫৭ সালের ১৩ মার্চ বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা প্রেসিডেন্ট ভবন আক্রমণ করে। কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এর পর একপর্যায়ে বিপ্লবীর হাতে পতন ঘটে বাতিস্তা সরকারের।
কাস্ত্রো বিপ্লবের পর ‘ইন্টিগ্রেটেড রেভ্যুলুশনারি অর্গানাইজেশন অব ২৬ মুভমেন্ট’ নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। ওই সময় পিপলস সোশ্যালিস্ট পার্টি তাকে সমর্থন করেছিল। ১৯৬২ সালের মার্চে তিনি গঠন করেন ‘ইউনাইটেড পার্টি অব দ্য কিউবান সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলেশন’। এই পার্টিই ১৯৬৫ সালের ৩ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে বলা ভালো, বাতিস্তা দু-দুবার ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৪০-৪৪ সাল পর্যন্ত একবার। ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টি তাকে সমর্থন করেছিল। জেনারেল বাতিস্তা ১৯৫২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর পর থেকেই তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন। ক্ষমতা দখল করে কাস্ত্রো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ চালান। ১৯৭৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হন। ২০০৮ সালে তিনি অবসরে যান। দেশটি এখন শাসন করছেন তার ছোট ভাই রাউল কাস্ত্রো। অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন, রাউল কাস্ত্রো ধীরে ধীরে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য তার দেশটি উন্মুক্ত করে দেবেন। তিনি দিয়েছেনও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা তিনি করছেন। গত ২১ জানুয়ারি দীর্ঘ ৫৪ বছরে বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবা আলোচনা শুরু করেছিল। হাভানায় পুনরায় মার্কিন দূতাবাস খোলা হয়েছে এবং ওবামা নিজে হাভানা সফর করেছেন। তবে সম্পর্কটি কোন পর্যায়ে গিয়ে উন্নীত হয়, সেটাও দেখার বিষয়। কিউবা কি ফিদেল কাস্ত্রো-পরবর্তী কিউবায় সমাজতন্ত্রকে পরিত্যাগ করবে? কিউবা কি আবারও বাজার অর্থনীতিতে ফিরে যাবে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে এসব প্রশ্ন উঠেছে এখন। বলা ভালো চিন ও ভিয়েতনামের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশও এই মুহূর্তে ধ্রুপদী মার্কসবাদ অনুসরণ করে না। সেখানে পরিবর্তন এসেছে। তাই খুব সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন এখনÑ কিউবা চিন বা ভিয়েতনামের পথ অনুসরণ করবে কিনা? ইতোমধ্যে ওবামা কিউবা সফর করেছেন (২০১৬)। এর আগে আরেকজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিউবা গিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে।
কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল কিউবার নিরাপত্তাহীনতা। যুক্তরাষ্ট্র কখনই কিউবায় একটি সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করে নেয়নি। বরং কিউবায় বিপ্লবের পর (১৯৫৯), কিউবা সরকার যখন লাতিন আমেরিকাজুড়ে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে চাইল, চে গুয়েভারা যখন ‘বিপ্লব’ সম্পন্ন করার জন্য কিউবা সরকারের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বলিভিয়ায় গেলেন (সেখানেই তাকে পরে হত্যা করা হয়), তখন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের কাছে ভিন্ন একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কখনই চায়নি, ‘তার প্রভাবাধীন এলাকায়’ অন্য কোনো ‘শক্তি’ প্রভাব খাটাক। ‘মনরো ডকট্রিন’-এর আদলে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে এ এলাকায় তথা লাতিন আমেরিকায় তার পূর্ণ কর্তৃত্ব। কিন্তু কিউবার বিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রের এই হিসাব-নিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা বিপ্লবের মাত্র দুবছরের মধ্যে ১৯৬১ সালে ভাড়াটে কিউবানদের দিয়ে কিউবা সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালায়। সিআইর অর্থে পরিচালিত এই অভিযান ‘বে অব পিগস’-এর অভিযান হিসেবে খ্যাত। বলাই বাহুল্য ওই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেমে থাকেনি। ঠিক এর পরের বছর ১৯৬২ সালের অক্টোবরে ‘কিউবা সংকট’ একটি পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছিল, কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে, যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছে, এটা বিবেচনায় নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র একটি নৌ-অবরোধ আরোপ করে, যাতে করে কিউবায় কোনো ধরনের সামরিক মারণাস্ত্র সরবরাহ করা না যায়। এই নৌ-অবরোধ অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দাবি করে, যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক থেকে তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে নিতে হবে। দীর্ঘ ১৩ দিন এই নৌ-অবরোধ বহাল ছিল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে মিসাইল প্রত্যাহার করে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নেয়। এর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে গেলেও সংকট থেকে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে এই অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে কিউবা ‘যুদ্ধ’ করে আসছে।
তবে দুদেশের মধ্যে এখনো বেশ কিছু বিষয়ে ন্যূনতম ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। ওবামার হাভানা সফরের সময়ও তা লক্ষ করা গেছে। মানবাধিকার ইস্যু কিংবা গুয়ান্তোনামো বে-তে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগার, কিউবায় রাজনৈতিক বন্দি ইত্যাদি ইস্যুতে দুই রাষ্ট্রপ্রধান হাভানায় সংবাদ সম্মেলনে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এসব ইস্যুতে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সংবাদ সম্মেলনে রাউল কাস্ত্রো জানিয়েছিলেন, তার দেশে কোনো রাজনৈতিক বন্দি নেই। গুয়ান্তোনামো বে কিউবার কাছে হস্তান্তর করারও কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি ওবামা। তবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের। কিউবার মানবাধিকারের অবনতি হয়েছে, এটাও স্বীকার করেননি কাস্ত্রো। স্পষ্টতই এসব ইস্যুতে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। যুক্তরাষ্ট্র যাদের ‘রাজনৈতিক বন্দি’ হিসেবে গণ্য করছে কিউবা তা করছে না। মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে দেখে, কিউবা সেভাবে দেখে না। ফলে মতপার্থক্য রয়েই গেছে। তবে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই মতপার্থক্য সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে একজন নয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে যাবেন। তার মনোভাবের ওপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। কাস্ত্রোর মৃত্যুর পর ট্রাম্প যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, তাতে একটি ইঙ্গিত আছে। কিউবা যতদিন তার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাবে, ততদিন রিপাবলিকান পার্টি নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস কিউবাকে এতটুকুও ছাড় দেবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে এমনটাই উঠে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ওবামার বক্তব্য ছিল অনেকটা ‘মডারেট’। তিনি কট্টর কোনো বক্তব্য দেননি।
একজন বিপ্লবীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার ধাঁচেই সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। সাফল্য তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি তিনি সফল ছিলেন, এটাও বলা যাবে না। মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ তিনি ৭ হাজার ডলারে উন্নীত করতে পেরেছিলেন, যা কিনা থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা জর্ডানের চেয়ে বেশি। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাও তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু অর্থনীতি আরও উন্নত, আরও বিনিয়োগের পরিস্থিতি উন্নত করতে পারত কিউবা। এখন ফিদেল নেই। হয়তো কিউবায় আরও পরিবর্তন আসবে ভবিষ্যতে। আদিওস কমরেড ফিদেল! বিদায় কমরেড ফিদেল!
Daily Amader Somoy
28.11.2016